মিয়ানমারে শক্তিশালী ভূমিকম্প, বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতখানি?
প্রকাশিত:
২৯ মার্চ ২০২৫ ১১:১৯
আপডেট:
১ এপ্রিল ২০২৫ ০০:৩১

২৮ মার্চ ২০২৫, দুপুরের দিকে মিয়ানমারে অনুভূত হওয়া ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পটি কেবল একটি দেশের ভূখণ্ডকেই কাঁপিয়ে দেয়নি, বরং এর তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত থাইল্যান্ড, চীন ও বাংলাদেশেও।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিমের সাগাইং শহরের কাছে। প্রথম কম্পনের ১২ মিনিট পরেই ছয় দশমিক চার মাত্রার আরেকটি কম্পন অনুভূত হওয়াতে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। এই শক্তিশালী ভূমিকম্পটি একদিকে যেমন প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূ-প্রাকৃতিক সংযোগের প্রমাণ দেয়, তেমনি অন্যদিকে একটি বৃহৎ আঞ্চলিক দুর্যোগের অশনি সংকেতও বহন করে আনে।
বিশেষত বাংলাদেশের জন্য এই ভূমিকম্প একটি সুস্পষ্ট বার্তা। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ক্রমবর্ধমান ভূমিকম্প প্রবণতা ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে এবং সেই ঝুঁকি মোকাবিলায় এখনই সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। মিয়ানমারে তুলনামূলকভাবে ঘন ঘন ভূমিকম্পের ইতিহাস বিদ্যমান।
১৯৩০ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে দেশটিতে সাত মাত্রার ছয়টি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল, যার সবগুলোই ছিল সাগাইং ফল্টের কাছাকাছি। ভূপৃষ্ঠের নিচের এই ফাটলটি মিয়ানমারের মাঝ বরাবর বিস্তৃত, যা এই অঞ্চলটিকে ভূমিকম্পের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল করে তুলেছে।
থাইল্যান্ড যদিও ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত নয়, সেখানে অনুভূত হওয়া বেশিরভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল এই প্রতিবেশী মিয়ানমারেরই। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল, মান্দালয়, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৫৯৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই দূরত্ব স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে।
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভূমিকম্পের ঝুঁকির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্বের সিলেট থেকে শুরু করে কক্সবাজার পর্যন্ত ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকা এবং হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চলগুলো ভূতাত্ত্বিকভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত। উদ্বেগের বিষয় হলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২০১৭ সালে বাংলাদেশ ও এর কাছাকাছি এলাকায় ২৮টি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১-এ এবং ২০২৪ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪-তে পৌঁছেছে। এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকম্পের সংখ্যা বাংলাদেশের জন্য সুস্পষ্ট বিপদ সংকেত। মিয়ানমারের আজকের শক্তিশালী ভূমিকম্পটি সেই বিপদ সংকেতকে আরও জোরালো করেছে এবং আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে অত্যাবশ্যকীয় করে তুলেছে।
ভূমিকম্প হলো একটি আকস্মিক ও বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর প্রভাবে ব্যাপক প্রাণহানি, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি আরও বেশি। দুর্বল নির্মাণ কাঠামো, ভূমিকম্প প্রতিরোধী বিল্ডিং কোডের অভাব এবং দুর্যোগ মোকাবিলার পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
মিয়ানমারের ভূমিকম্পটি আমাদের সেই ভয়াবহতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মিয়ানমারে আজকের শক্তিশালী ভূমিকম্পটি এই অঞ্চলের ভূ-কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আন্তঃসীমান্ত দুর্যোগের ভয়াবহতাকে আরও একবার সামনে নিয়ে এসেছে। একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও হয়, তার প্রভাব বাংলাদেশে অনুভূত হতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, দুর্বল অবকাঠামো এবং দুর্যোগ মোকাবিলার অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি এই তিনটি প্রধান কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দুর্বল।
ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরগুলোয় অসংখ্য বহুতল ভবন রয়েছে, যাদের অনেকেই ভূমিকম্পের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়নি। বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে অনুসরণ না করা এবং নির্মাণকালে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার প্রবণতা এই ভবনগুলো ভূমিকম্পের সময় ধসের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।
এছাড়া সরু রাস্তাঘাট এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন ভূমিকম্পের পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে যদি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে, তবে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনহানি এবং সম্পদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, মিয়ানমারের আজকের ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য একটি জরুরি সতর্কবার্তা।
এখন সময় এসেছে ভবিষ্যতের জন্য আরও জোরালো প্রস্তুতি নেওয়ার। দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়া হয়তো সবসময় সম্ভব নয়, কিন্তু দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অবশ্যই সম্ভব। সংকট মোকাবিলা করার জন্য এখনই সামগ্রিক ও সুদূরপ্রসারী প্রস্তুতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই প্রস্তুতিকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বেশি নজর দেওয়া উচিত।
ভূমিকম্পের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন: বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলো আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। ভূতাত্ত্বিক গবেষণা এবং ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর একটি বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন। বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্পের প্রভাবে কোন এলাকায় কেমন ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন করা জরুরি। এই ঝুঁকি মূল্যায়ন আমাদের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করবে।
অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিল্ডিং কোডের কঠোর প্রয়োগ: বাংলাদেশের অবকাঠামো, বিশেষ করে ভবন নির্মাণে ভূমিকম্প প্রতিরোধী নিয়মকানুন কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিদ্যমান বিল্ডিং কোডকে যুগোপযোগী করা এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পুরোনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো শক্তিশালীকরণ অথবা ভেঙে নতুন করে ভূমিকম্প সহনীয় কাঠামোয় নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার, প্রকৌশলী, স্থপতি এবং সাধারণ জনগণ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি: ভূমিকম্পের পূর্বে, ভূমিকম্পের সময় এবং ভূমিকম্পের পরে কী করণীয় এই বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করা প্রয়োজন, যাতে মানুষ ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে। দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। খাদ্য, পানীয় জল, ওষধ এবং অন্যান্য জরুরি সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলাও জরুরি।
প্রযুক্তি ও গবেষণার ব্যবহার: ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যদিও এখনো একটি দুরূহ কাজ, তবে আধুনিক প্রযুক্তি এবং গবেষণার মাধ্যমে ঝুঁকির মাত্রা এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে ভূমিকম্প নিয়ে আরও বেশি গবেষণা এবং উন্নত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা এবং জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করতে পারি।
জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ: ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং এর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে এবং কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে প্রচারণা চালানো উচিত।
স্থানীয় কমিউনিটিগুলোয় স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করে তাদের প্রাথমিক উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি পরিবারকে দুর্যোগ মোকাবিলা পরিকল্পনা তৈরি করতে উৎসাহিত করা উচিত, যেখানে পরিবারের সদস্যরা ভূমিকম্পের সময় কোথায় আশ্রয় নেবে এবং কীভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকবে।
আঞ্চলিক সহযোগিতা: ভূমিকম্প একটি আঞ্চলিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আজকের মিয়ানমারের ভূমিকম্পটি তার প্রমাণ। তাই দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ঝুঁকি হ্রাসের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারত এবং অন্যান্য ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং যৌথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রযুক্তি এবং জ্ঞানের আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি দেশ একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে এবং নিজেদের প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে পারে।
আর্থিক প্রস্তুতি: ভূমিকম্পের মতো বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। দুর্যোগের পরবর্তী পুনর্বাসন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য একটি জাতীয় দুর্যোগ তহবিল গঠন করা উচিত। এই তহবিলে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং সাধারণ মানুষ সবারই সাধ্যমত অবদান রাখা উচিত। এছাড়া দুর্যোগ বীমা এবং অন্যান্য আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা উচিত, যাতে দুর্যোগের শিকার ব্যক্তি এবং পরিবার দ্রুত তাদের জীবন পুনর্গঠন করতে পারে।
মিয়ানমারে আজকের ভূমিকম্পটি বাংলাদেশের জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা। আমরা যদি এই মুহূর্তে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ না করি, তাহলে ভবিষ্যতে একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের আঘাতে আমাদের দেশ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ মহল এবং সাধারণ জনগণ সকলের সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগই পারে এই ঝুঁকি মোকাবিলা করতে এবং একটি দুর্যোগ সহনীয় বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।
আজকের ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভূমিকম্পের ঝুঁকি কোনো দূরের বিষয় নয়, বরং আমাদের দোরগোড়ায় উপস্থিত। এখন যদি আমরা সম্মিলিতভাবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিই, তবে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে।
বাংলাদেশের সরকার, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের উচিত এই মুহূর্তের গুরুত্ব অনুধাবন করে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে, একটি সুদূরপ্রসারী এবং সমন্বিত প্রস্তুতিই পারে ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলে আমাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে।
ড. সুজিত কুমার দত্ত ।। অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]
সম্পর্কিত বিষয়:
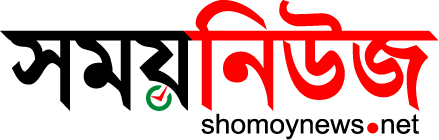





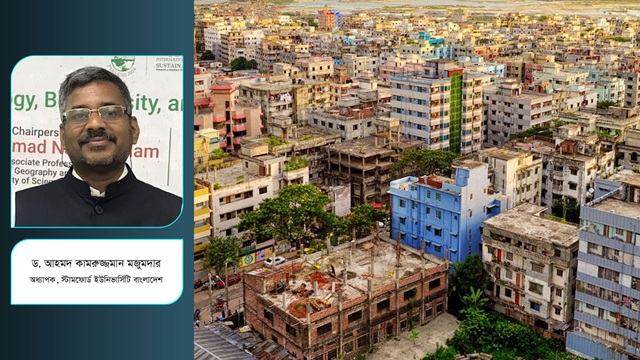

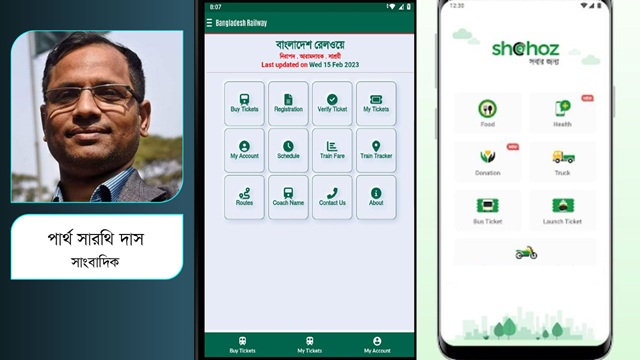
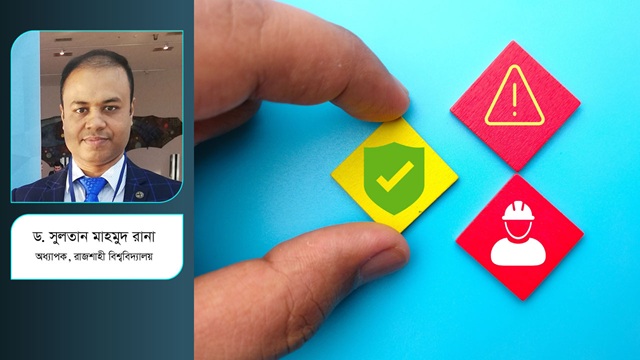
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: