শূন্য বেকারত্ব যেভাবে সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করবে
প্রকাশিত:
১৫ এপ্রিল ২০২৫ ১২:০৫
আপডেট:
১৬ এপ্রিল ২০২৫ ২২:২৮

বেকারত্বের ইতিহাস বিশ্ব অর্থনীতি, শিল্প, শ্রমবাজার এবং বৈশ্বিক ঘটনাবলির (যেমন যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মন্দা) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।
প্রথমত, শিল্প বিপ্লব-পূর্ব যুগ (১৮শ শতাব্দীর আগে)। এই সময়ে বেকারত্বের ধারণা তেমন প্রচলিত ছিল না। অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ বা ছোটখাটো ঘরোয়া শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কাজ ছিল ঋতুভিত্তিক এবং কর্মহীন সময়েও মানুষ কোনো না কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। সেসময় শ্রমবাজার সংগঠিত না থাকায় বেকারত্বের আধুনিক ধারণা কার্যত অনুপস্থিত ছিল।
দ্বিতীয়ত, শিল্প বিপ্লবের যুগ (১৮শ থেকে ১৯শ শতাব্দী)। শিল্প বিপ্লব ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার শ্রমবাজারে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বৃহৎ পরিসরের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ফলে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত বহু মানুষ কাজ হারায়। এতে শহরকেন্দ্রিক বেকারত্ব এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বেকারত্বের সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে।
বিশ্বব্যাপী একাধিক মহামন্দা বেকারত্বে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দায় ১৯২৯ সালের শেয়ারবাজার ধসের পর যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব ২৫ শতাংশে পৌঁছায়, আর জার্মানিতে ব্যাপক বেকারত্ব চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের (যেমন নাৎসি দলের উত্থান) অনুঘটক হয়। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে গৃহঋণ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতনে কোটি কোটি মানুষ চাকরি হারায়। স্পেন ও গ্রিসে যুব বেকারত্ব ৫০ শতাংশে ছাড়িয়ে যায়।
সর্বশেষ, কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানে ভয়াবহ সংকট তৈরি করে। স্বাধীনতার পর নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের পথে। প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক হলেও বেকারত্ব, বিশেষত তরুণদের মধ্যে, এখনো বড় সমস্যা।
সরকারি তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে বেকারত্বের হার ৫.৩ শতাংশ, তবে এতে আধা-বেকারত্ব ও লুকানো বেকারত্ব প্রতিফলিত হয় না। বিশেষত, গ্রামীণ কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজের অভাব ও দক্ষতার অপচয় স্পষ্ট।
এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যাকে বলে দারিদ্র্যের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব (Poverty Paradox)। এটি এমন একটি বাস্তবতা যেখানে দারিদ্র্য নিরসনে প্রচেষ্টা ও সম্পদ বিনিয়োগ করলেও সমস্যাটি টিকে থাকে বা আরও বাড়ে। অনেক দারিদ্র্য বিমোচন নীতি স্বল্পমেয়াদি সহায়তায় সীমাবদ্ধ থাকে—যেমন খাদ্য বিতরণ বা নগদ অর্থ সহায়তা—কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে দারিদ্র্য দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে।
এই বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব বেকারত্বকেও ভয়াবহ করে তোলে। অনেক সময় কাজ থাকা সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না, যা লুকানো বেকারত্বের শামিল। প্রতিষ্ঠানগুলো এ ফাঁদকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হলেও ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সুফল আসে না। এটি প্রচলিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে তোলে।
বেকারত্বকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। খোলা বেকারত্ব হলো যেখানে মানুষ সক্রিয়ভাবে কাজের সন্ধানে থাকে। আধা বেকারত্ব হলো এমন অবস্থা, যেখানে কেউ কাজ পেলেও তা তার দক্ষতা বা প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট নয়—যা দারিদ্র্যের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রত্যাশিত বেকারত্ব স্বল্পস্থায়ী, যা সাধারণত পেশা পরিবর্তনের সময় ঘটে।
সবচেয়ে ভয়াবহ হলো কাঠামোগত বেকারত্ব, যা তখন সৃষ্টি হয় যখন অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে কর্মসংস্থানের ধরনে বড় পরিবর্তন আসে। যেমন, কৃষি থেকে শিল্প খাতে স্থানান্তরের ফলে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে, কারণ তারা নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। অনেক বিশ্লেষকের মতে, বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ বেকারত্ব বিদ্যমান, অর্থাৎ অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। তাই, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ছাড়া এই সংকট নিরসন সম্ভব নয়।
বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যার ভয়াবহতা বুঝতে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির দিকে তাকালেই যথেষ্ট। এটি বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,১০০-এরও বেশি মানুষ বসবাস করে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মোট জন্মহার হ্রাস পেয়েছে, তবুও তা অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বেশি। একই সঙ্গে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার চাপ আরও বেড়েছে।
দেশটির কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ প্রায় ৩০ শতাংশ, যারা ৩৫ বছরের কম বয়সী, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সম্ভাবনা তৈরি করলেও, কর্মসংস্থানের অভাবে তা বেকারত্বের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সামনের বছরগুলোয় এই সংকট আরও তীব্র হতে পারে, যা বাংলাদেশকে বৈশ্বিকভাবে উচ্চ বেকারত্বের দেশের তালিকায় শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়লেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সে অনুপাতে তৈরি হচ্ছে না। শিক্ষাব্যবস্থা শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় বহু শিক্ষিত তরুণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাচ্ছে না। বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে অনেকেই দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না, যা তাদের চাকরির সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে।
দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এখনো কৃষিনির্ভর, যেখানে কাজের স্থায়িত্ব ও আয় নিশ্চিত নয়। বর্ষা বা কৃষির অফ-সিজনে অনেক মানুষ বেকার হয়ে পড়ে, যা আংশিক বেকারত্ব বাড়ায়। শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, অধিকাংশ শিল্প এখন মেশিন নির্ভর হয়ে যাওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হচ্ছে।
ঢাকাসহ প্রধান শহরগুলোয় চাকরির সুযোগ থাকলেও গ্রামীণ ও দূরবর্তী এলাকায় তা অত্যন্ত কম। ফলে শহরমুখী অভিবাসন বাড়ছে, যা নগর এলাকায় জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি করছে এবং গ্রামীণ বেকারত্ব বাড়াচ্ছে। এই কাঠামোগত সমস্যাগুলো সমাধান না হলে ভবিষ্যতে বেকারত্ব আরও প্রকট হতে পারে।
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শূন্য বেকারত্ব রূপকল্প বেকারত্ব সংকট মোকাবিলার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন, যা শুধু কর্মসংস্থান তৈরি করার ওপর নয়, বরং মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার সামর্থ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়। তার মতে, বেকারত্ব দূর করার প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে প্রত্যেকেই নিজেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং কোনো ব্যক্তি চাকরির অভাবে কষ্ট পাবে না।
এই রূপকল্পের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো সামাজিক ব্যবসার ধারণা, যেখানে ব্যবসার মূল লক্ষ্য হবে শুধু লাভ অর্জন নয়, বরং কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান করা। এই ধরনের ব্যবসা লাভজনক হলেও এর মুনাফা মালিকদের মধ্যে ভাগাভাগি করা হয় না; বরং তা পুনরায় বিনিয়োগ করা হয় নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে এবং আরও বেশি মানুষকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য। এই ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্যবসা কেবল মুনাফার জন্য পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।
শূন্য বেকারত্ব অর্জনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উদ্যোক্তা তৈরি করা। ইউনূস মনে করেন, মানুষকে শুধু চাকরির জন্য অপেক্ষা করা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। বিশেষত তরুণ প্রজন্ম এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে এবং একই সঙ্গে অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।
উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার এই পথকে সহজ করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে তারা ছোট পরিসরে ব্যবসা শুরু করতে পারবে, যা একদিকে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে, অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে নতুন কর্মসংস্থান গড়ে তুলবে।
তরুণদের বিশেষভাবে এই রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ড. ইউনূস বলেন, তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে। চাকরির জন্য অপেক্ষা না করে, তারা যেন নিজেদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান বের করতে পারে এবং সেই সমাধানকে ব্যবসায়িক কাঠামোর মাধ্যমে প্রসারিত করতে পারে, সেটিই তার অন্যতম লক্ষ্য।
এই রূপকল্পের সবচেয়ে উদ্ভাবনী অংশ হলো চাকরি সৃষ্টির প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি। সাধারণত কর্মসংস্থান তৈরি করা বলতে বোঝানো হয় যে সরকার বা বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেবে এবং মানুষের জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু ড. ইউনূস এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র সরকারি নীতি বা কর্পোরেট চাকরির ওপর নির্ভরশীলতা বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বরং ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে, স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিত করে এবং সেগুলোর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব।
এই রূপকল্প বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এক নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে, যেখানে চাকরির অভাবে কেউ আর নিরুপায় থাকবে না। বিশেষত দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার জন্য এটি একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে। যদি সরকার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, এবং তরুণ উদ্যোক্তারা একসঙ্গে এই মডেল বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে, তাহলে বাংলাদেশে বেকারত্ব মোকাবিলা করা সম্ভব হবে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হবে।
শূন্য বেকারত্ব ধারণাটি অনুপ্রেরণামূলক হলেও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ বিশাল। এটি ধরে নেয় যে সবাই চাকরি পাবে বা উদ্যোক্তা হবে, কিন্তু বাস্তবে দক্ষতা, মূলধন ও ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা সবার নেই। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান দুর্বল, চাকরির সংস্কারে আন্দোলন হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে প্রজন্ম ব্যবসাবিমুখ। সামাজিক ব্যবসার মডেল আদর্শিক, যা নিরক্ষর ও পৃষ্ঠপোষক সংস্কৃতির সমাজে অবাস্তব। অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বাধা এ লক্ষ্যকে কঠিন করে তোলে। ফলে, বাংলাদেশের মতো বাস্তবতায়, শূন্য বেকারত্ব অর্জন করা এখনও অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এবং এর বাস্তবায়ন অদূর ভবিষ্যতে কঠিন হতে পারে।
ড. এ কে এম মাহমুদুল হক ।। অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত বিষয়:
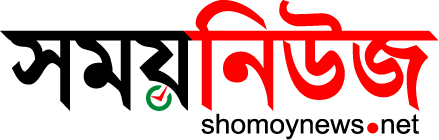


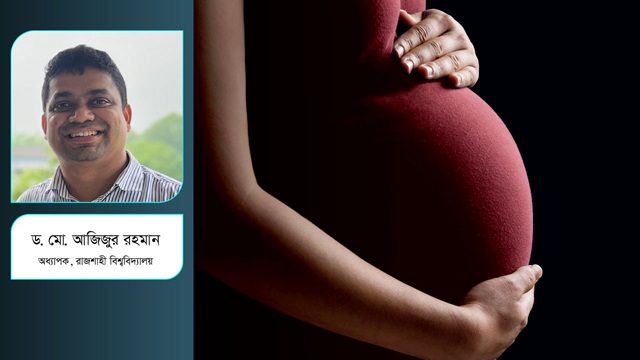
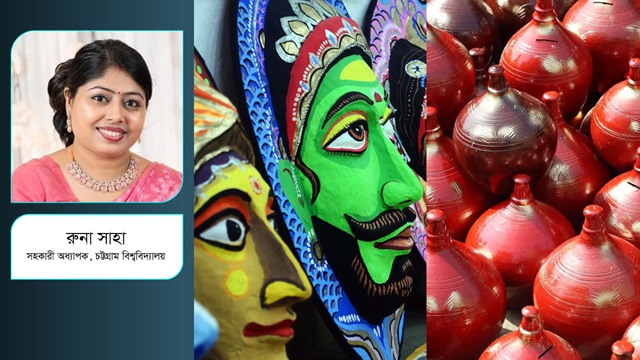




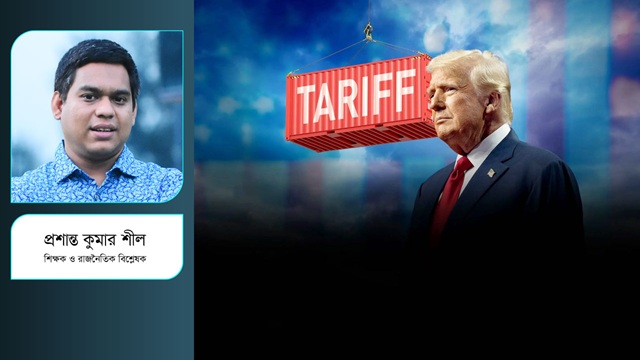
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: