চৈত্র সংক্রান্তির বিক্ষত দিন
প্রকাশিত:
১৩ এপ্রিল ২০২৩ ১৭:৪০
আপডেট:
১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ০৯:৪৫
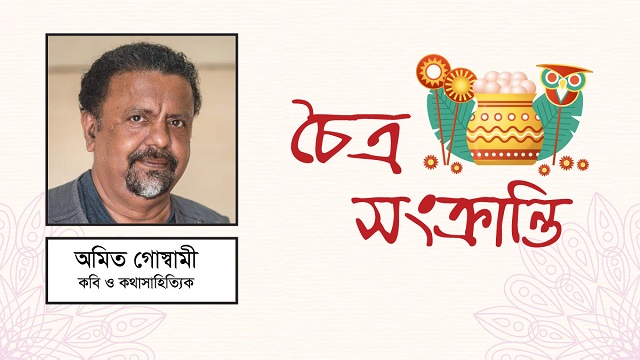
দাদু-ঠাকুমা-নানা-নানিদের কোলেপিঠে মানুষ হওয়ার সুযোগ এখন তাদের জোটে কোথায়? কালের অগ্রগতিতে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে হারিয়ে যায় সংস্কার ও সংস্কৃতি। কিন্তু কলকাতায় থেকেও আমার চোখে চৈত্রসংক্রান্তির চিত্র নিখুঁতভাবে এঁকে দিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা।
তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মানুষ। তিনি চৈত্র সংক্রান্তি এলেই গল্পের প্যান্ডোরা বাক্স খুলে বসতেন। তার জন্ম পাবনা জেলার কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে সংক্রান্তির ভোর থেকে শুরু হয়ে যেত নববর্ষের উৎসব। নদীতে স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে বাড়ির সকলের সঙ্গে হাজির হতে হতো ঠাকুরঘরে।
সেই সময় কোনো উৎসবে গৃহদেবতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ঠাকুরঘরে প্রদীপ, ধূপ জ্বালিয়ে ভাইয়ের হাতে তিনি তুলে দিতেন যবের ছাতু। বাড়ির প্রত্যেক সদস্যকে সেদিন যবের ছাতু খেতেই হবে। বছরের শেষ বিকেলটাও ভারি মজার। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কুলোর বাতাসে ছাতু ওড়ানোর সময়।
মেয়েরা সুর করে ছড়া কাটছেন, ‘শত্রুর মুখে দিয়া ছাই, ছাতু উড়াইয়া ঘরে যাই’। চৈত্রের শুকনো বাতাসে মেঠো পথের ধুলো আর ছাতু মিলেমিশে একাকার। এর পরেই শুরু হতো নদীর জলে একে অপরকে ভিজিয়ে দেওয়ার খেলা। বছরের শেষ সূর্যকে সাক্ষী রেখে সেই খেলা চলতো সন্ধ্যা পর্যন্ত।
তিনি বলতেন, ‘চৈত্র সংক্রান্তিকে আমার বলতাম ছাতু সংক্রান্তি। সেই দিনের অনুষ্ঠান ছিল অনেকটা ভাইফোঁটার মতো। ভাইয়ের হাতে ছাতু দেওয়ার ওই অনুষ্ঠানকে বলা হতো ভাই-ছাতু।’
এপার-ওপার দুই বাংলা জুড়েই চৈত্র সংক্রান্তির হরেক নাম। পঞ্জিকাতে এই দিনটি মহাবিষুব নামে চিহ্নিত। বাকি নামগুলোর সঙ্গে একটা করে উৎসবের ছোঁয়া থেকে গিয়েছে। কোথাও পাঁচকুমার, কোথাও ফলগছানো, কোথাও এয়ো সংক্রান্তি, কোথাও আবার মধু সংক্রান্তি। নানা ব্রত-পার্বণের মধ্য দিয়ে বছরের শেষ দিন থেকেই নতুন বছরের উৎসবের সুরটা বেঁধে দেওয়া হতো। তবে এই দিনটি গাজন উৎসব নামে সম্যক পরিচিত।
গাজন বা চড়ক বাংলা বছরের শেষ উৎসব। জাতপাতের ভেদাভেদ ও সামাজিক কৌলীন্য ভেঙে যে কেউ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। শুধু শিবকে কেন্দ্র করে নয়, গাজন উৎসব পালিত হয় ধর্মরাজকে কেন্দ্র করেও। গাজন শব্দটির উৎপত্তি গর্জন থেকে। কেউ কেউ মনে করেন সন্ন্যাসীদের হুঙ্কার রব শিবসাধনায় গাজন রূপেই প্রচলিত।
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে উল্লেখ মেলে—‘চৈত্র মাস্যথ মাঘেবা যোহর্চ্চয়েৎ শঙ্করব্রতী। করোতি নর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্রবানি দিবাশিনম্।। মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশ সপ্তদিনানি বা। দিনমানং যুগং সোহপি শিবলোক মহীয়তে।।’
এর অর্থ চৈত্রে কিংবা মাঘে এক-সাত-দশ-পনেরো কিংবা তিরিশ দিন হাতে বেতের লাঠি নিয়ে শিবব্রতী হয়ে নৃত্য ইত্যাদি করলে মানুষের শিবলোক প্রাপ্ত হয়। পুরাণের এই উল্লেখ চড়ক কিংবা গাজন উৎসব রূপে পালিত হয়। গাজন উৎসবের মূলত তিনটি অংশ— ঘাট-সন্ন্যাস, নীলব্রত ও চড়ক। আগে মূলত চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই ভক্তরা সন্ন্যাস পালন করতেন। এখন কেউ চৈত্র সংক্রান্তির সাতদিন আগে, কেউ বা তিনদিন আগে থেকে কঠোর নিয়ম পালন করেন।
সন্ন্যাস পালন করা হয় বলে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, হবিষ্যি গ্রহণ আবশ্যিক। একটি দলের মধ্যে একজন মূল সন্ন্যাসী এবং একজন শেষ সন্ন্যাসী রূপে গণ্য হন। উৎসবে এই দু’জনেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বাংলার একেক প্রান্তে দেখা যায় গাজনের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য।
গাজনের পরের দিন পালিত হয় নীল পূজা। গ্রামবাংলার মহিলারা সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই দিন গাজনের সন্ন্যাসীদের ফল, আতপচাল ও অর্থ দান করেন। চৈত্রের শেষ দিনে উদযাপিত হয় চড়ক উৎসব। এই উৎসবেরও কিছু নিয়ম আছে। যেমন, চড়ক গাছটিকে শিবমন্দিরের কাছের কোনো পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। সন্ন্যাসী সেটিকে তুলে আনেন গাজনতলায়।
তারপরে চড়কগাছ পূজা করে তা চড়কতলায় পোঁতা হয়। এরপরে শুরু হয় মূল চড়কের অনুষ্ঠান। প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের ওপরে অনেকটা উঁচুতে আংটায় ঝুলে থাকা জনা দু’য়েক সন্ন্যাসীর ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়ার পরিচিত দৃশ্য।
ঘুরপাক খেতে খেতে আচমকাই ঝুলে থাকা সেই দুই সন্ন্যাসী নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উদ্দেশে ছুড়ে দিচ্ছেন বেল, কাঁচা আম ইত্যাদি ফল। সেই ফল কে ধরবে সেই নিয়ে শুরু হয় হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি। সেই ফল হাতে ধরাও নাকি ভাগ্যের ব্যাপার! এমনটাই বিশ্বাস মানুষের। মালদহ জেলার গম্ভীরা উৎসব, ত্রিপুরার বৈসু উৎসব, তালতলার শিরনি, গ্রাম বাংলার শাকান্ন উৎসব সবই চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব।
গাজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন। যেমন আগুনঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, ঝুলঝাঁপ, বানফোঁড়া, কপালফোঁড়া ইত্যাদি। এক সময় চড়ক প্রথাটিকেই অমানুষিক আখ্যা দিয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারিরা।
১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫-র মধ্যে ছোটলাট বিডন এই প্রথা রোধ করেছিলেন। শোনা যায়, সেই থেকেই সন্ন্যাসীরা চড়কগাছে পাক খেতে পিঠে গামছা বেঁধে উঠতে শুরু করে। সেই সময়ের কাঁসারিপাড়ায়, কাঁসারিরা সঙ বের করতো। অশ্লীলতার দায়ে এক সময় তাও বন্ধ হয়ে যায়।
তখনকার চড়ক উৎসব প্রসঙ্গে সবচেয়ে মজার বর্ণনা আছে কালীপ্রসন্ন সিংহ’র ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-য়। তিনি লিখেছেন…
“…রাস্তায় লোকারণ্য, চারদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সূতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুঁড়ে একবারে মরিয়া হয়ে নাচ্তে নাচ্তে কালীঘাট থেকে আস্চে।…চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠল।…এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্তা বাঁশের বাঁশি, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া নেকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি করতে বসেছে…।
এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচ্তে নাচ্তে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে— মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখনও ছেড়ে, পা নড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল ‘দে পাক দে পাক’ শব্দ। কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস! একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখছেন।”
তবে চৈত্র সংক্রান্তির সবচেয়ে দুর্বিষহ বর্ণনা শুনেছি আমাদের পাড়ার এক পরিবারে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বয়স্ক মহিলার বিলাপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। বর্ণনা আমার মনে দগদগে ক্ষত হয়ে আজও আছে কারণ তখন আমি নয় বছরের বালক। ১৯৭১ সাল। যুদ্ধ শুরু হয়েছে পূর্ব বাংলায়। সম্ভবত গ্রামের নাম খানপোতা। জেলা খুলনা। গ্রামে নয়-দশ ঘর হিন্দু। বাকিরা মুসলমান। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব নেই।
মুসলমানরা হিন্দুদের আগলে রেখেছিল চোখের মণির মতো। চারিদিক থমথমে হলেও সেই গ্রামে তখনো একটাও গুলি চলেনি। এতই প্রত্যন্ত অঞ্চল যে সৈন্য কেন, পুলিশের টিকিও দেখা যায় না। সেই গ্রামের মানুষেরা জানে যে হানাহানি একটা চলছে বটে তার জের এতদূরে বোধহয় আসবে না। বরং গ্রাম ছাড়া বিপদ। রাস্তায় কোথায় কী ঘটে। তারচেয়ে বাপদাদার ভিটেতে বাস করা ভালো।
ইতিমধ্যে এসে পড়ল চৈত্র সংক্রান্তি। এলাকার মুসলমানরা হিন্দুদের বলল, এবার তোমরা চড়ক করবে না? আলোচনায় স্থির হলো চড়ক হবে। চৈত্র সংক্রান্তির অপরাহ্ণে চড়ক উৎসব শুরু হলো। কানাই-বলাই দুই ভাই পিঠে আঁকশি এঁটে উঠে পড়ল চড়কের চড়কিতে। চড়কের ঘূর্ণি ঘুরছে বনবন করে। পিঠের বেঁধা আঁকশি দিয়ে নিচে রক্ত পড়ছে টুপটুপ করে। নদীর ধারে এই মচ্ছবে গ্রামবাসী চেঁচাচ্ছে – দে পাক, দে পাক।
কানাই বলাইয়ের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারাও ঈশ্বর ভক্তিতে পিঠে বেঁধা আঁকশির যন্ত্রণা টের পাচ্ছে না। হঠাৎ ট্যাঁর – ট্যাঁর শব্দ। গুলি চলছে। কখন গানবোটে করে পাক হানাদার বাহিনী হাজির হয়েছে কেউ টের পায়নি। হানাদার সেনারা ব্রাশ ফায়ার করছে। লুটিয়ে পড়ছে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের মানুষ। বেশিরাই মুসলমান। কানাই বলাই ওপরে চড়কিতে ঘুরছে। তাদের রক্ত পড়তে দেখে হানাদার সেনারা ভেবেই ফেলেছিল হয়তো এদের মেরে গ্রামবাসীরা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাই কানাই বলাইয়ের ওপরে গুলি চালায়নি।
চোখের সামনে গুলি চলতে দেখে, দলেদলে মানুষ মরতে দেখে তারা আর সামলাতে পারেনি। ঝুলন্ত অবস্থায় চেঁচিয়ে বলে উঠল – জয় বাংলা, পাকিস্তান মুর্দাবাদ। মুহূর্তে মেশিনগানের নল উঠল ওপরে।
ঝুলন্ত অবস্থায় গুলি ফুঁড়ে দিল দুই ভাইকে। দূর থেকে মা দেখলেন সব। তারপরে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় ভাইয়ের বাসায়। তার বিলাপধ্বনি আর বর্ণনা আজও কানে ভাসে। কিন্তু এই কান্না, বিলাপ ও বর্ণনার পরে কখনো তিনি বলতে ভুলতেন না—জয় বাংলা। আচ্ছা, এদের কথা কখনো লেখা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে?
অমিত গোস্বামী ।। কবি ও কথাসাহিত্যিক
সম্পর্কিত বিষয়:
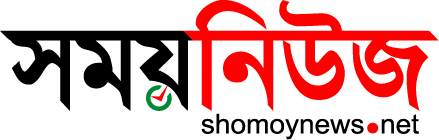


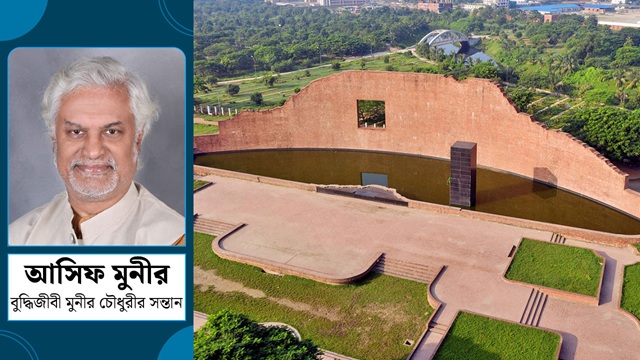

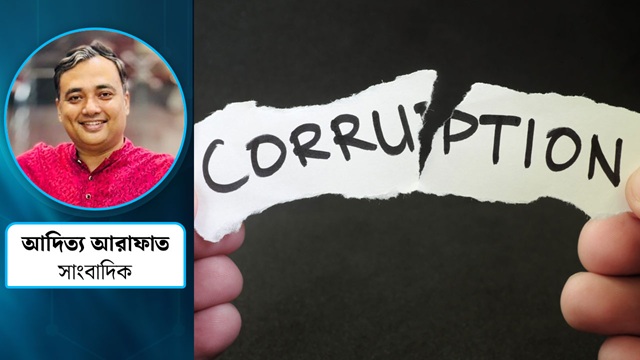





আপনার মূল্যবান মতামত দিন: