বাতাসে বাড়ছে সিসা, পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় কী?
প্রকাশিত:
২ ডিসেম্বর ২০২৪ ১১:১০
আপডেট:
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ০৪:৪১

সিসা একটি নীরব ঘাতক। সিসা দূষণের বিষয়টি আমাদের অনেকের জানা নেই। এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিসাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
ইনস্টিটিউট অব হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের (আইএইচএমই) [Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)] ধারণা মতে, সিসা দূষণের কারণে বিশ্বের প্রায় ১০ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু ঘটেছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোয় তুলনামূলকভাবে মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি।
বিষাক্ত ধাতু সিসা বেশ সহজলভ্য এবং হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের ফলে এটি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন উপায়ে মানুষ সিসার সংস্পর্শে আসছে।
সিসা একটি বিষাক্ত ভারী পদার্থ। যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সিসা খুব অল্প তাপে গলে যায় এবং বাষ্পীভূত হয়। ফলে একে বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে গুণগত মান উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য-পানীয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও চামড়া এ তিনটি উপায়ে সিসা মানবদেহে প্রবেশ করে।
এটা শরীরে রক্তের সঙ্গে মিশে যকৃৎ, কিডনি, হাড়সহ সবকিছুই আক্রান্ত করে। এটা দেহের কোমল পেশিতন্ত্রগুলো আক্রান্ত করে। রক্তে এটি ছয় থেকে সাত সপ্তাহ অবস্থান করে। মানুষের শরীরে সিসা প্রবেশ করলে তা সহজে অবমুক্ত হয় না। সিসা মূলত আমাদের হাড় ও দাঁতে জমা হয়। যেখানে এটি ২০ থেকে ৩০ বছর থাকতে পারে।
পরিবেশের অন্যান্য দূষণ আমরা সহজে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন পানি দূষণে স্বাদ, গন্ধ ও রঙের পরিবর্তন দেখা যায়। বায়ু দূষণে চোখ ঝাপসা বা নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কিন্তু সিসা দূষণ একেবারে নীরবে ঘটে। এটি খালি চোখে চিহ্নিত করা যায় না।
সব ধরনের দূষণে সিসা একটি অনুঘটক। পানি, বায়ু ও মাটি দূষণেও সিসা পাওয়া যায়। এটি নিয়ন্ত্রণে ২০০৬ সালে প্রথম পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীনে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ সংক্রান্ত আইন আছে। কিন্তু সব বিষয় আইনের আওতাভুক্ত নয়। যুক্তরাষ্ট্রে সিসাযুক্ত রং ব্যবহারে বিধিনিষেধ দিয়ে আইন আছে।
প্রতিটি দূষণের সঙ্গে সিসার সম্পৃক্ততা আছে। তাই সংশ্লিষ্ট সব আইনে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সিসা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এ সংক্রান্ত নীতিমালায় ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনার কথা বলা আছে। আমাদের দেশে এগুলো বাস্তবায়ন একটু কঠিন। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে দুটি সিসা কারখানা বন্ধের খবর এসেছে।
দেশের পরিবেশগত সব সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ভার পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর। এককভাবে তাদের পক্ষে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরে লোকবল সংকট ও কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয় রয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় খুবই জরুরি। সিসা দূষণ রোধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক হয়ে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা দরকার। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়া ইউনিসেফের একটি প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে সমাধানের আরও পথ পাওয়া যাবে।
শিশুদের ব্যবহারের লাল ও হলুদ রঙের পেনসিলেও প্রচুর সিসা রয়েছে। সিসামুক্ত রং তৈরির উপকরণে পাঁচগুণ বেশি খরচ হয়। তাই সিসামুক্ত রঙের উপকরণের ওপর শুল্ক কমানো দরকার।
যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৮ সালে আবাসস্থলে সিসা মিশ্রিত রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক দেশ রঙে সিসার পরিমাণ কমানোর জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত অন্তত ৭৬টি দেশে সিসা মিশ্রিত রঙের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় এবং ব্যবহারের বিষয়ে কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতা নেই।
স্বল্পমূল্যের ব্যাটারিচালিত মোটরযানের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে এলআইসিতে লেড-অ্যাসিড ব্যাটারির ব্যবহার মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সব লেড-অ্যাসিড ব্যাটারিই পুরোনো ব্যাটারি পুনরায় চক্রায়ন এবং ফেলে দেওয়া ধাতু থেকে তৈরি করা হয়। ব্যাটারিতে ব্যবহৃত সিসার প্রায় পুরোটাই পুরোনো হওয়ার পরও তা পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় চক্রায়ন করা সম্ভব।
পুরোনো ব্যাটারিগুলো গলিয়ে অশোধিত সিসা পাওয়া যায়, যা নতুন ব্যাটারি তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উন্নত দেশের গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারিসহ ই-বর্জ্যগুলো অনুন্নত দেশগুলোয় রপ্তানি করে দেওয়া হয়, যার বেশিরভাগই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার অপ্রাতিষ্ঠানিক সিসা কারখানায় জায়গা করে নেয়, যা সেই অঞ্চলকে অতিরিক্ত সিসা দূষণের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়।
একদিকে অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের উচ্চ চাহিদা আর অন্যদিকে পুনরায় চক্রায়ন বাজার থেকে বিপুল পরিমাণে এর সরবরাহের কারণে বর্তমান পৃথিবীতে বিশাল এক অ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মৃৎশিল্পেও তৈজসপত্র চকচকে করার কাজে সিসার প্রলেপ ব্যবহার করা হয়।
লেড ক্রোমেট হচ্ছে বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় এমন একটি সস্তা রাসায়নিক হলুদ রং, যা নিয়মিত ঘরোয়া খাবার তৈরিতে ব্যবহারের ফলে তা সিসা দ্বারা দূষিত হচ্ছে। হলুদের ব্যবসায়ীরা যে নিম্নমানের শিকড় বিক্রি করে এবং সিসা মিশ্রিত খারাপ মানের হলুদ গুঁড়া বাজারে এনে নিজেদের লাভের পাল্লা ভারী করে।
ডিজেল ও পেট্রলে সিসা যুক্ত থাকে। যদিও ২০২৪ সালে বৈশ্বিকভাবে সিসাযুক্ত পেট্রলের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। সিসা দূষণের ক্ষতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে সচেতনতার বিকল্প নেই।
আমাদের দেশে ব্যাটারিগুলো রিসাইকেল করার ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢাকায় নির্দিষ্ট কিছু স্থান থাকলেও পরিপূর্ণ রিসাইকেল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। আবার ব্যাটারি থেকে সিসা গলিয়ে যখন আলাদা করা হয়, তখন সিসার অংশবিশেষ বিভিন্নভাবে মাটি ও পানি দূষণ ঘটায়। ব্যাটারিগুলোয় যে সিসার প্লেট থাকে, সেগুলো ভাঙা হয় আবার ব্যবহার করার জন্য।
সিসা গলানোর সময় যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, তাতে কিছু পরিমাণ সিসা বাতাসে মিশে যায়। পরে নিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। আবার গলিত সিসা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। পরে এই সিসা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। শস্যদানা ও চাষ করা মাছের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে।
গর্ভাবস্থায় সিসার সংস্পর্শে এলে শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তার দৃষ্টি, শ্রবণ এবং শিখন বিকাশগত সমস্যা থেকে শুরু করে আচরণগত সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে করা পরিসংখ্যানমতে, যেসব শিশুর রক্তে ২.৪-১০ মাইক্রোগ্রাম বা ডেসিলিটার মাত্রায় সিসার উপস্থিতি থাকে, তাদের বুদ্ধিমত্তা কম, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা কম কৃতকার্য হয় এবং পুরো জীবনকালে কম অর্থ আয় করে।
যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) রক্তে সিসার ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রা ৬০ মাইক্রোগ্রাম বা ডেসিলিটার থেকে ৫ মাইক্রোগ্রাম বা ডেসিলিটার-এ নামিয়ে এনেছে। যদিও রক্তে সিসার উপস্থিতির ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণিত নিরাপদ মাত্রা নেই; বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে এমন কোনো মাত্রা নেই। মূল কথা হলো, সমস্যার বা ঝুঁকির মাত্রা বাড়তে থাকে যত বেশি উচ্চ মাত্রার সিসা ব্যবহার করা হবে এবং সংস্পর্শে আসা হবে।
সিসা দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। সিসা দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি শিশুর শরীরে উচ্চমাত্রার সিসা রয়েছে। সিসা দূষণের ফলে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
গবেষণায় দেখা যায়, সিসাজনিত শুধু বুদ্ধিমত্তা ঘাটতির ফলে মানবসম্পদের নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতার কারণে দেশে বছরে ১ লাখ ২৮ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এই পরিমাণ বাংলাদেশের গড় অভ্যন্তরীণ সম্পদের (জিডিপি) ৬ শতাংশ। আমাদের দেশের শিশুরা খর্বাকৃতির হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে সিসা দূষণের সম্পর্ক থাকতে পারে।
বিআইসিসিতে ‘আন্তর্জাতিক সিসা দূষণ প্রতিরোধ সপ্তাহ’ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় সিসামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়।
বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০ কোটি শিশুর রক্তে উচ্চমাত্রায় সিসা আছে। এদের বেশিরভাগই নিম্ন আয়ের দেশে বসবাসরত। কারণ, সেখানে সিসার অধিক ব্যবহার এবং দূষণ হয়ে থাকে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মতো পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। বেশিরভাগ শিশুই এশিয়া এবং আফ্রিকার, তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোয়ও এই অনুপাত কম নয়।
সিসা দূষণ শিশুদের ছোট বয়সে স্বাস্থ্য এবং বিকাশের ওপর বহুমুখী এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে, যার জন্য সারা জীবন ধরে তাদের ভুগতে হয়। এমনকি প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সিসার বিষাক্ততা শিশুর মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে, যা কিনা নিপীড়ন এবং অপরাধ করার মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মূল কারণ।
উৎপাদনশিল্পে নিয়ম এবং সতর্কতা মেনে চলাই এই ক্ষতি ঠেকানোর প্রধান উপায়। তাই কঠোর নিরাপত্তা বিধির মাধ্যমে সব ধরনের উৎসে সিসা দূষণ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা প্রয়োজন। সিসার সংস্পর্শে আসা কমাতে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন সব শিশু নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, পড়াশোনার সুযোগ পায় এবং পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় বেড়ে ওঠে। এসব উদ্যোগ খুব দ্রুত নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যত বেশি সময় ধরে মানুষ সিসার সংস্পর্শে থাকবে, ততই স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।
বিশেষজ্ঞদের মতে সিসা মোকাবিলায় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন—
১। সিসা দূষণের সব উৎস চিহ্নিত করা প্রয়োজন;
২। শিল্পপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ের রঙে সিসা দূষণ রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুসরণ করতে হবে;
৩। সিসাযুক্ত যেকোনো উপকরণে অতিরিক্ত শুল্কারোপ করে সিসার আমদানি ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে;
৪। সিসার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করা দরকার;
৫। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সিসা দূষণ রোধ করতে হবে;
৬। সিসাযুক্ত ব্যাটারি পুনরায় চক্রায়ন কারখানাগুলো নিয়মিত নজরদারিতে নিয়ে আসা প্রয়োজন;
৭। সিসা দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করা জরুরি;
৮। মসলা, খাদ্যদ্রব্য, গয়না, খেলনা ও রান্নার সরঞ্জামে সিসার ব্যবহার বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;
৯। সিসার মাত্রা পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করা প্রয়োজনো;
১০। সিসা দূষণ রোধে গবেষণাও জরুরি;
১১। রক্তে সিসা শনাক্তকরণ কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে নেওয়া দরকার
১২। এ সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় জরুরি।
লেখকঃ গবেষক ও অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
সম্পর্কিত বিষয়:
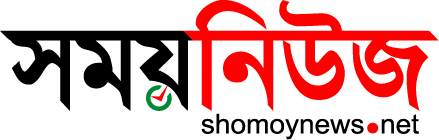


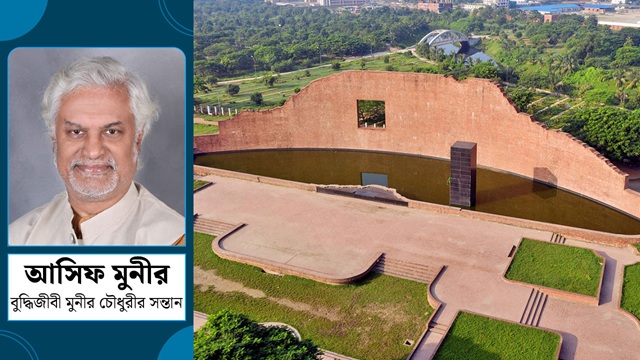

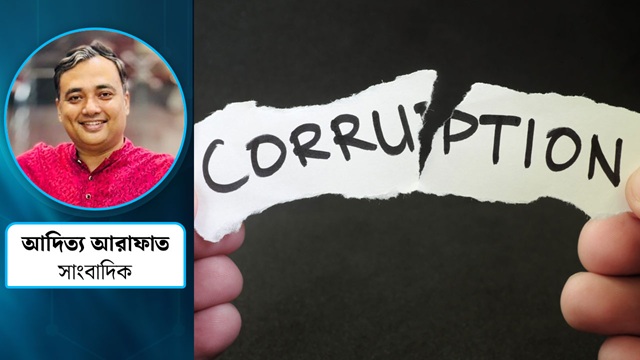





আপনার মূল্যবান মতামত দিন: