টেকসই ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা জরুরি কেন?
প্রকাশিত:
২ মে ২০২৫ ১২:৩৪
আপডেট:
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ০৩:৪৫

বিশ্বব্যাপী ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো বিপুল পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পরিচালনা করে। প্রতি বছর প্রায় ৩৮০ বিলিয়ন ঘনমিটার বর্জ্য পানি উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে উচ্চ মাত্রায় রাসায়নিক উপাদান, যেমন নাইট্রোজেন ও ফসফরাস, থাকে। এগুলো প্রাণীজ পরিবেশে ইউট্রোফিকেশন (অতিরিক্ত পুষ্টির কারণে জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি) ঘটায়।
আশ্চর্যের বিষয় হলো, উৎপাদিত বর্জ্য পানির আনুমানিক ৮০ শতাংশ এখনো অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় সরাসরি পরিবেশে নিষ্কাশিত হয়, যা প্রায়ই ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে, ফলে জলদূষণ এবং পরিবেশগত ক্ষতি বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, অপ্রক্রিয়াজাত বর্জ্য পানি বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মিষ্টি পানির উৎসকে দূষিত করছে। যদিও ড্রেনেজে সলিড বর্জ্যের মোট পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন, তথাপি প্রতিদিন প্রায় ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্লাস্টিক বর্জ্য মহাসাগরে প্রবাহিত হচ্ছে, যা পরিবেশগত ক্ষতি, ড্রেন ব্লকেজ এবং মাইক্রোপ্লাস্টিকের সমস্যা সৃষ্টি করছে।
এছাড়াও, শহুরে ড্রেনেজ সিস্টেমে বিপুল পরিমাণ সেডিমেন্ট জমা হয়। যদিও অনেক এলাকায় এর পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা হয়নি, তথাপি জানা যায় যে কিছু এলাকায় এটি ড্রেনেজের ক্ষমতা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়, যার ফলে বন্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ শহর দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে নিয়মিতভাবে বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
১৯০০ সালের পূর্বে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত সরল, স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ এবং মূলত অতিরিক্ত পানি ও বর্জ্য অপসারণের জন্য ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে, যেমন সিন্ধু সভ্যতা (মহেঞ্জোদারো), রোমান সাম্রাজ্য ও মিসরীয় সভ্যতায় উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়—যেখানে পাথর বা ইটের তৈরি ড্রেনের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি ও বর্জ্য দূরে সরিয়ে দেওয়া হতো। তবে এসব ব্যবস্থা শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক উন্নত সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল; গ্রামীণ এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিতই ছিল।
মধ্যযুগীয় ইউরোপে ড্রেনেজ ছিল খুবই অপর্যাপ্ত—রাস্তাঘাটের খোলা নালার মধ্য দিয়ে বর্জ্য ও পানি প্রবাহিত হতো, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করত। তখন বৃষ্টির পানি ও মলবর্জ্যের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না—সবকিছু আশেপাশের খাল, নদী বা জলাশয়ে সরাসরি ফেলা হতো, কোনো প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই।
শিল্পবিপ্লবের সময়ে (১৮শ শতকের শেষ থেকে ১৯শ শতক পর্যন্ত) নগরায়ণের ফলে ড্রেনেজ সমস্যার প্রকটতা আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে লন্ডনের মতো শহরে ১৮৫৮ সালের ‘গ্রেট স্টিঙ্ক’ ও কলেরার মহামারির পর ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর থেকেই শহরগুলোতে ভূগর্ভস্থ স্যুয়ারেজ সিস্টেম গড়ে উঠতে শুরু করে, যা আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।
উনিশ শতকের পূর্বে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অপরিকল্পিত, খোলা নালা ও প্রাকৃতিক খাল নির্ভর, যেখানে বৃষ্টির পানি ও বর্জ্য একসাথে অপসারণ করা হতো এবং তা কোনো প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই নদী বা খালে ফেলে দেওয়া হতো—ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য তা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াত। অপরদিকে, বর্তমানের ড্রেনেজ ব্যবস্থা অনেক বেশি পরিকল্পিত, প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব।
এখন শহরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন, আলাদা স্টর্ম ড্রেন ও স্যুয়ারেজ লাইন, এবং পানি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আধুনিক প্লান্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেন্সরভিত্তিক নজরদারির মাধ্যমে জলাবদ্ধতা ও দূষণের সমস্যা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হচ্ছে। ফলে ড্রেনেজ ব্যবস্থার দিক থেকে বর্তমান সময় অতীতের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত, টেকসই এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠেছে।
কিছুটা ইতিহাস তুলে ধরার কারণ হলো, এটি বোঝানো যে বাংলাদেশের ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা এখনও প্রায় দুই শতাব্দী পুরোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থার মতোই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে শুধু ঢাকা শহরের অবদান প্রায় ৬৯ শতাংশ। এই বর্জ্যের গঠনে ৭৪.৪ শতাংশ জৈব পদার্থ, ৩.৫ শতাংশ প্লাস্টিক, ৯.১ শতাংশ কাগজ, ১.৫ শতাংশ ধাতু এবং ৮ শতাংশ অন্যান্য উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তবে এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের সঠিক সংগ্রহ, পরিবহন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ঢাকা শহরে প্রতিদিন উৎপন্ন বর্জ্যের মাত্র ৫০ শতাংশ সঠিকভাবে অপসারণ করা হয়; বাকী ৫০ শতাংশ রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে, যা দুর্গন্ধ ও পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মীরা প্রায়ই কোনো ধরনের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করেন, ফলে তারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হন।
বিশ্বের সফলতম দেশগুলোর একটি হলো সিঙ্গাপুর, যেখানে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত কার্যকর ও উন্নত। দেশটি একটি সমন্বিত ড্রেনেজ এবং বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, যা শুধু বন্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে না, বরং পানির গুণগত মানও উন্নত করে। ‘অ্যাকটিভ, বিউটিফুল, ক্লিন (ABC) ওয়াটারস’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর ড্রেন এবং জলাধারগুলোকে আকর্ষণীয় স্থানে রূপান্তর করেছে, একইসঙ্গে বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনাও কার্যকরভাবে পরিচালনা করছে।
সিঙ্গাপুরের অবকাঠামোতে রয়েছে উন্নত ভূগর্ভস্থ ড্রেন, জলাধার এবং SMART টানেল, যা ভারী বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি সড়ক টানেলের কাজও করে। এছাড়া, টেকসই সমাধান হিসেবে দেশটি জল প্রবাহ শোষণকারী রাস্তা ও বৃষ্টি-বাগান ব্যবহার করে, যা ড্রেনেজ সিস্টেমের উপর চাপ কমায়।
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, স্মার্ট মনিটরিং প্রযুক্তি এবং সরকারের বড় ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর একটি অত্যন্ত প্রতিরোধক্ষম এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তবে মনে রাখতে হবে, সিঙ্গাপুর একটি ছোট আয়তনের এবং তুলনামূলকভাবে ধনী দেশ। তাই তাদের জন্য সফল হওয়া যতটা সহজ, বাংলাদেশের মতো বৃহৎ এবং অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দেশের জন্য সেই সফলতা অর্জন করা ততটা সহজ নয়।
তবে শহরের আকার ও জটিলতার দিক থেকে লন্ডনের ড্রেনেজ ব্যবস্থা শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম সফল উদাহরণ। এর সূচনা ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ১৮৫৮ সালের ‘গ্রেট স্টিঙ্ক’ পরবর্তী সময়ে হয়, যখন থেমস নদীতে অপরিষ্কার শৌচাগার বর্জ্যের কারণে ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য সংকট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার স্যার জোসেফ বাজালগেট একটি বিস্তৃত ভূগর্ভস্থ স্যুয়ার নেটওয়ার্ক ডিজাইন করেন। ১৮৭০-এর দশকে এই সিস্টেমটি সম্পন্ন হলে, তা সেই সময়ের জন্য এক বৈপ্লবিক উদ্ভাবন হয়ে ওঠে, যা থেমস নদী থেকে শৌচাগারের বর্জ্য সরিয়ে জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে নাটকীয় উন্নতি আনে।
পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে এই ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত ও আধুনিকীকৃত হয়েছে, যাতে শহরের বাড়তে থাকা জনসংখ্যা ও চাহিদা মোকাবিলা করা যায়। বর্তমানে, থেমস টাইডওয়ে টানেল নামে একটি ‘সুপার স্যুয়ার’ নির্মাণাধীন, যা পুরানো ভিক্টোরিয়ান সিস্টেমের অতিরিক্ত চাপ কমাতে এবং অতিবৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে সহায়তা করবে। আজকের দিনে লন্ডনের ড্রেনেজ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং টেকসই পদ্ধতি, যেমন বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও প্রবাহ শোষণকারী পেভমেন্ট, ব্যবহার করা হয়।
এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারী বৃষ্টিপাতের প্রভাবে সম্ভাব্য বন্যা প্রতিরোধে ফ্লাড ব্যরিয়ারসহ নানা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সবমিলিয়ে, লন্ডনের ড্রেনেজ ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক অর্জন এবং আধুনিক, টেকসই নগর ব্যবস্থাপনার সফল উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এখন আসা যাক, বাংলাদেশ এখান থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে। প্রথমত, বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার প্রতি কখনোই যথাযথ গুরুত্ব প্রদর্শন করেননি। শুধু ড্রেনেজ ব্যবস্থাই নয়—শহরের সম্প্রসারণ বলতে আমরা বুঝি উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণ আর আশপাশের কৃষিজমিকে দখল করে হাউজিং প্রকল্প গড়ে তোলা। বড়জোর দু-এক লেনের রাস্তা নির্মাণই আমাদের ‘উন্নয়ন’ বোঝার পরিধি।
আরবান সেফটি প্রটোকলের মতো ধৈর্য্যধারণকারী, ব্যয়বহুল, টেকসই ও নৈতিক পরিকল্পনার কথা চিন্তা করার মতো সচেতনতা বা দূরদর্শিতা এই জাতির কখনোই ছিল না, এবং অদূর ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ এবং ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০০৮ সালে দেশের পৌরসভাগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ইতিমধ্যে ২৫৬টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি পৌরসভাগুলোর কাজ চলমান রয়েছে।
এই পরিকল্পনাগুলো প্রণয়নে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৩২ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু নানা প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এসব ব্যয়বহুল মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফলে, দেশের পৌরসভাগুলো, যেগুলো মূলত গ্রামীণ শহর হিসেবে বিকশিত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলোও দিন দিন অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে, আর সমস্যা আরও গভীরতর হচ্ছে।
উক্ত পরিকল্পনাসমূহ কাগজে-কলমেই পড়ে থাকবে, কারণ এসব পরিকল্পনা যারা করেছেন, তাদের বেশিরভাগের উদ্দেশ্য কখনোই বাস্তবায়ন ছিল না। পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে যে সম্মানী পাওয়া যাবে, মূলত সেই উদ্দেশ্যেই এইসব কাজ করা হয়েছে। শুধু আমলারা নন, গবেষকরাও টেকসই ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনাকে একটি গালভরা শব্দে পরিণত করেছেন এবং এই ছত্রছায়ায় লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
তাদের তৈরি করা গবেষণা প্রতিবেদনগুলো হয়তো সুন্দরভাবে বাধাই করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো প্রকাশের পর সেগুলোর পুনঃমূল্যায়ন বা পর্যালোচনা করা হয়নি। আসলে, অনেক সময় সেসব রিপোর্টে এমন কার্যকরী দিকনির্দেশনা বা সুপারিশ থাকে না, যা বাস্তবে প্রভাব ফেলতে পারে। বেশিরভাগ গবেষণা সামাজিক গবেষণার কাঠামো অনুসরণ করলেও, কিছু ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
এজন্য বলা যায়, বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা একটি ‘বুদ্ধিবৃত্তিক সৌখিনতা’তে রূপ নিয়েছে—যেখানে আমলা ও গবেষক উভয়েই এক ধরনের ব্যক্তিগত লাভের খেলায় মত্ত। সুতরাং, এই দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সমাধান চাইলে বাংলাদেশকে প্রথমেই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে হবে। মনোভাবের এই রূপান্তর ছাড়া টেকসই ড্রেনেজ ব্যবস্থা কিংবা প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের দিকে দৌড় কোনো বাস্তব ফল দেবে না। মূল পরিবর্তন শুরু হতে হবে চিন্তা ও দায়বদ্ধতার স্তর থেকে, প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়ন আসবে পরে।
ড. এ কে এম মাহমুদুল হক ।। অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত বিষয়:
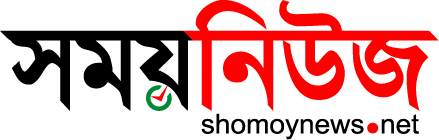


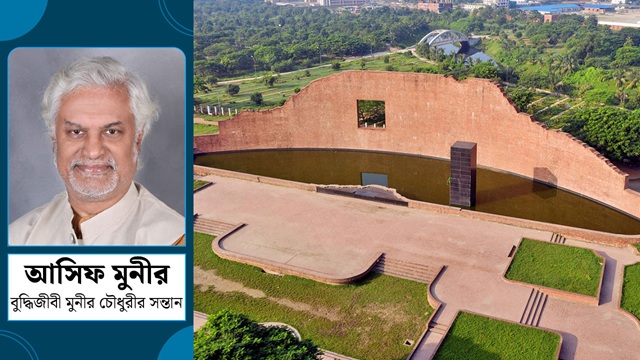

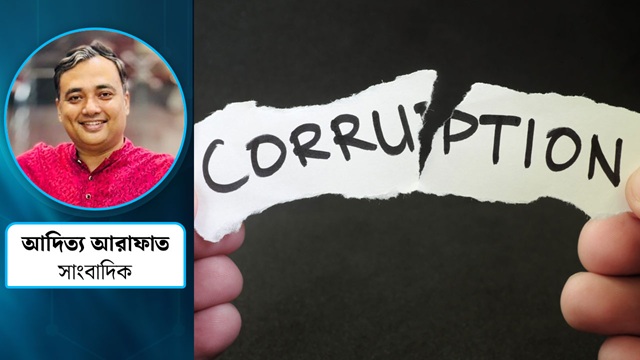





আপনার মূল্যবান মতামত দিন: