নীরব মহামারি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, ঠেকানো সম্ভব?
প্রকাশিত:
১৭ মে ২০২৫ ১০:৩২
আপডেট:
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ০৩:৪২

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা জীবাণুনাশকের প্রতিরোধী ক্ষমতা সারা বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্বে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ‘নীরব মহামারি’ শুরু হয়েছে। ২০২২ সালে বিখ্যাত ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা বলছে, শুধুমাত্র ২০১৯ সালে প্রায় ১২ লাখের অধিক মানুষ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।
ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার না করা গেলে এবং রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার ঠেকাতে সারা বিশ্ব একযোগে কাজ না করলে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি মানুষ এর কারণে মৃত্যুবরণ করবে।
অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল হলো সেসব যৌগ, যা ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস বা পরজীবীর বিরুদ্ধে কাজ করে। যেসব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে তাদের ‘অ্যান্টিবায়োটিক’ বলা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে, এরা অন্য ধরনের জীবাণু যেমন ছত্রাক, ভাইরাস এবং পরজীবীকে ধ্বংস করতে সক্ষম নয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এমন একটি অবস্থা যখন কোনো রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে ধ্বংসের জন্য নির্ধারিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের ডোজ সেসব জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে না অর্থাৎ, এটি হলো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের উপস্থিতিতে জীবাণুর বেঁচে থাকার সক্ষমতা।
সম্প্রতি স্বাস্থ্য গবেষকগণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স’ শব্দটি বেশি ব্যবহার করলেও সাধারণ মানুষের কাছে ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স’ শব্দটি অধিক পরিচিত। এর কারণ, চিকিৎসায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় অ্যান্টিবায়োটিক।
অন্যান্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল যৌগ যেমন ছত্রাকনাশক, ভাইরাসনাশক বা পরজীবীনাশকের ব্যবহার কম হয় এবং এ ধরনের ওষুধের প্রতি প্রতিরোধিতা তৈরির হার কম, তাই ‘অ্যান্টিফাংগাল রেজিস্ট্যান্স’ বা ‘অ্যান্টিভাইরাল রেজিস্ট্যান্স’ আলাদা করে এতটা পরিচিত পায়নি। এ লেখায় আমি মূলত ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স’ নিয়ে আলোচনা করব, কারণ, রেজিস্ট্যান্সঘটিত মৃত্যুর জন্য মূলত এটিই দায়ী।
প্রশ্ন হলো, ব্যাকটেরিয়া কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ওঠে? বর্তমানে দেশে যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো মানুষ ও প্রাণীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর একটি বড় অংশ কীভাবে প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে উঠলো? এদের কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা? আমাদের করণীয় কী?
ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতা বা রেজিস্ট্যান্স অতি প্রাচীন। মাটির যেসব ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে তারা যাতে তাদের নিজের উৎপাদিত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে নিজে ধ্বংস না হয়ে যায়, সেজন্য তাদের জিনোমের মধ্যে এমন কিছু রেজিস্ট্যান্স জিন বহন করে যেগুলোর কাজ হলো অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াকে সুরক্ষা দেওয়া।
বিজ্ঞানীদের ধারণা, অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ায় থাকা এ রেজিস্ট্যান্স জিনগুলো আনুভূমিক জিন স্থানান্তরের (horizontal gene transfer) তিনটি পদ্ধতি- transformation, transduction এবং conjugation- এর মাধ্যমে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বিভিন্নভাবে বিস্তার ঘটেছে।
যদিও বিজ্ঞানীরা অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ায় রেজিস্ট্যান্সের জন্য দায়ী জিনের স্থানান্তর হয়েছে এমন শক্ত প্রমাণ এখনো পাননি। তাই, রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ায় রেজিস্ট্যান্সের জন্য দায়ী জিনগুলোর উৎস প্রাথমিক উৎস এখনো অজানা। তবে, আনুভূমিক জিন স্থানান্তরের উক্ত পদ্ধতি তিনটি ব্যবহার করে এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ায় রেজিস্ট্যান্স জিন স্থানান্তর করার ঘটনা প্রমাণিত।
যেকোনো উৎস থেকে যে পদ্ধতিতেই হোক কোনো রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ায় রেজিস্ট্যান্ট জিন স্থানান্তরের পর ব্যাকটেরিয়াগুলো ‘সিলেকশন প্রেশার’-এর কারণে সে জিনগুলো নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে এবং অন্য ব্যাকটেরিয়ায় তাদের প্রতিরোধী জিনগুলো ছড়িয়ে দেয়।
অ্যান্টিবায়োটিকের সিলেকশন প্রেশার হলো এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী বা রেজিস্ট্যান্ট জিনের বিস্তার ত্বরান্বিত হয়। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, মানুষ ও প্রাণীদেহে এবং উদ্ভিদে অ্যান্টিবায়োটিকের অতিব্যবহার এবং অপব্যবহার এ পদ্ধতিকে তরান্বিত করছে।
ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হওয়ার আরেকটি পদ্ধতি হলো মিউটেশন নামক এক ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসার সময় দেহে থাকা ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জিনের মিউটেশন ঘটিয়ে প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি করে এবং মিউটেশন হওয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো বেঁচে যায়।
এই বেঁচে যাওয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো দ্রুত বংশবিস্তার করে এবং ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণ ডোজে আর কাজ করে না। তখন, ভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করাতে হয় বা উচ্চ ডোজের প্রয়োজন পড়ে, যা রোগীর জন্য নিরাপদ নাও হতে পারে।
ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের জন্য প্রফিল্যাকটিক হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিকের যৌক্তিক ব্যবহারের পাশাপাশি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার ও ভুল ব্যবহার হয় জীবনরক্ষাকারী এ ওষুধটির।
বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের এ ধরনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য অধিকাংশ ওষুধের মতো অ্যান্টিবায়োটিক একটি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রয় নিষিদ্ধ, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি হয় প্রায় ৪০ শতাংশ।
বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত যে, অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার (যেমন- সঠিক নিয়মে বা ডোজে ব্যবহার না করা, অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট না করা), অপব্যবহার (যেমন- দ্রুত ওজন বাড়ানোর জন্য ফার্মের পশু-পাখিতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা; রোগের কারণ না জেনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা) এবং অতিব্যবহার (যেমন- ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ যেমন ঠাণ্ডা লাগা, ফ্লু ইত্যাদিতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা) ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠার মূল কারণ। তার মানে হলো, অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাই হলো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলার অন্যতম উপায়।
তবে, অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি খুব সহজ নয়। আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার, অপব্যবহার এবং অতিব্যবহারের জন্য শুধু সাধারণ মানুষ, ওষুধের দোকানদার এবং হাতুড়ে ডাক্তাররা দায়ী নন। এর জন্য চিকিৎসকদের কিছু অংশ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি, ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায় রয়েছে।
বিশ্বের সব দেশে প্রায় ২৫ বছর ধরে ‘অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ’ চালু হলেও, আমাদের দেশে এখনো এটি চালু হয়নি। অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ হলো একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক, নিরাপদ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুর বিস্তার কমানো, রোগীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং অ্যান্টিবায়োটিকের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা বজায় রাখা।
হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ফার্মেসিতে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হলে অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহার, অপব্যবহার এবং অতিব্যবহার কমতে বাধ্য। তবে, গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট ছাড়া ফার্মেসিতে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ চালু করা অসম্ভব। সরকার সম্প্রতি ৭০০ সরকারি ফার্মেসি চালু করার এবং সেগুলোয় গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার তখন চাইলে সেসব ফার্মেসিতে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ চালু করতে পারে।
অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রামের একটি অন্যতম টুলস হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অ্যান্টিবায়োটিকের ‘AWaRe (Access, Watch, Reserve)’ শ্রেণিকরণ পদ্ধতি এবং এ শ্রেণিকরণ বিবেচনায় নিয়ে চিকিৎসায় সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণ করা। ২০১৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের চিকিৎসায় বা প্রতিরোধে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণ করতে অ্যান্টিবায়োটিকের ‘AWaRe’ শ্রেণিকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করে, যা ২০২৩ সালে আপডেট করা হয়।
উক্ত শ্রেণিকরণ পদ্ধতিতে বর্তমানে বিশ্বে ব্যবহৃত ২৫৭টি অ্যান্টিবায়োটিককে Access, Watch এবং Reserve- তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। অ্যাক্সেস (Access) ক্লাসের অ্যান্টিবায়োটিকসমূহের (যেমন- অ্যামক্সিসিলিন, ডক্সিসাইক্লিন ইত্যাদি) বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধী ক্ষমতা বা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করার ক্ষমতা কম, ওয়াচ (Watch) ক্লাসের অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ (যেমন- অ্যাজিথ্রোমাইসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইত্যাদি) বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত প্রতিরোধিতা বা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতে সক্ষম এবং রিজার্ভ (Reserve) ক্লাসের অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ (যেমন- মেরোপেনেম, লাইনেজোলিড ইত্যাদি) অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করলে ‘last-resort’ বা ‘শেষ ভরসা’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা হলো AWaRe ক্লাসের অ্যান্টিবায়োটিকের অ্যাক্সেস গ্রুপের ৬০ শতাংশ, ওয়াচ গ্রুপের ৪০ শতাংশ এবং রিজার্ভ গ্রুপের ১০ শতাংশের বেশি অ্যান্টিবায়োটিক মুখে খাওয়া যাবে এমন ডোসেজ ফর্ম যেমন- ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ বা সাসপেনশন হিসেবে উৎপাদন করা যাবে না। কিন্তু, বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভিন্ন।
সম্প্রতি এলসভিয়ার প্রকাশনীর ‘Journal of Infection and Public Health’-এ প্রকাশিত ‘Assessment of the Bangladeshi antibiotic market: Implications of the WHO AWaRe classification and dosage form availability on antimicrobial resistance’ শীর্ষক আমাদের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৮১টি অ্যান্টিবায়োটিকের জেনেরিক বাজারজাত করা হয়।
আমরা দেখিয়েছি, এই ৮১টি অ্যান্টিবায়োটিক জেনেরিকের ৫৪.৩২ শতাংশ হলো ‘Watch’, ৩০.৮৬ শতাংশ ‘Access’ এবং ৮.৬৪ শতাংশ ‘Reserve’ ক্লাসের। বাকি ৬.১৭ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক এ তিনটি ক্লাসের মধ্যে পড়ে না।
আমাদের গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে বাজারজাত করা ২৫টি অ্যাক্সেস গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের ৮৮ শতাংশ, ওয়াচ গ্রুপের ৪৪টি অ্যান্টিবায়োটিকের ৭৫ শতাংশ এবং রিজার্ভ গ্রুপের ৭টি অ্যান্টিবায়োটিকের ২৮.৫৭ শতাংশ মুখে খাওয়া উপযোগী ডোসেজ ফর্মে উৎপাদন করা হয়, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে অ্যাক্সেস গ্রুপের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ, ওয়াচ গ্রুপের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ এবং রিজার্ভ গ্রুপের ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ বেশি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা গেলে জীবনরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার অনেকাংশে কমে আসবে। কারণ, ইনজেকশন বা সরাসরি রক্তে দেওয়া স্যালাইনের ব্যবহার করতে দক্ষ নার্স বা চিকিৎসকের প্রয়োজন পড়বে।
আমাদের গবেষণায় চিন্তিত হওয়ার মতো আরেকটি বিষয় উঠে এসেছে। তা হলো, দেশের বাজারে ওয়াচ এবং রিজার্ভ গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (CAGR)। ২০২২ সালে দেশে যে ১৫টি অ্যান্টিবায়োটিকের সবচেয়ে বেশি বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল তার মধ্যে সাতটি অ্যান্টিবায়োটিক ছিল ওয়াচ গ্রুপের এবং পাঁচটি ছিল রিজার্ভ গ্রুপের।
রিজার্ভ গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর উচ্চ প্রবৃদ্ধি ভীষণ উদ্বেগজনক, কারণ, এগুলো অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসায় শেষ ভরসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ শ্রেণির যে সাতটি অ্যান্টিবায়োটিক দেশে বাজারজাত করা হয় সেগুলোর অতিব্যবহার বা ভুল ব্যবহারের কারণে রেজিস্ট্যান্স ছড়িয়ে পড়ছে।
এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুঘটিত রোগের চিকিৎসায় আর কোনো উপায় থাকবে না। ফলে, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে লাখ লাখ মানুষ।
আশঙ্কার বিষয় হলো, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ‘The Microbe’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, রিজার্ভ গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক মেরোপেনেম এবং কলিস্টিনের বিরুদ্ধে Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii-সহ কয়েকটি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ইতিমধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে এবং তা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের Institute of Epidemiology, Disease Control & Research (IEDCR) ২০২৩ সালে ‘National Antimicrobial Resistance (AMR) Surveillance Report, Bangladesh’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখানো হয়েছে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের রোগীদের থেকে সংগ্রহ করা তিনটি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া- E. coli, K. pneumoniae এবং A. baumannii-এর ৪৮-৬৪ শতাংশ আইসোলেট মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ক্ষমতা অর্জন করেছে। কোনো জীবাণু যখন তিনের অধিক রাসায়নিক শ্রেণির অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে কাজ করে না তখন তাকে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বলা হয়।
উন্নত যে দেশগুলোয় যেখানে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রাপ্যতা কল্পনা করা যায় না এবং যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রামগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেখানে অ্যামক্সিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিনসহ অনেক অ্যান্টিবায়োটিক এখনো প্রায় কার্যকরী। যেমন- যুক্তরাজ্যে এখনো ৯০ শতাংশ E. coli আইসোলেটের বিরুদ্ধে সিপ্রোফ্লক্সাসিন অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকরী, কিন্তু, বাংলাদেশে এর হার মাত্র ৫ শতাংশ। এ দুই দেশে অ্যাম্পিসিলিন, কারবাপেনেমসহ অন্য অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রেও কার্যকারিতার বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষণীয়।
তবে, বাজারের যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো হুমকির মধ্যে বা আর কাজ করছে না, সেগুলোর কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। কারণ, রেজিস্ট্যান্স অনেক ক্ষেত্রে রিভার্সিবল প্রক্রিয়া। গবেষণা বলছে, অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার, ভুল ব্যবহার ও অতিব্যবহার বন্ধ করলে সিলেকশন প্রেশার কমে আসবে, ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের মধ্যে ধরে রাখা রেজিস্ট্যান্ট জিনগুলো ছেড়ে দিয়ে হালকা হতে চাইবে এবং এর ফলে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা পুনরায় ফিরে আসবে।
তাই, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ চালু করতে হবে এবং AWaRe শ্রেণিকরণ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে হবে। আরেকটি কার্যকরী উপায় হলো, উন্নত রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক রোগী থেকে অন্য রোগীতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু সংক্রমিত না হয়। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভীষণ পস্তাতে হবে কোনো সন্দেহ নেই।
ড. মো. আজিজুর রহমান ।। অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]
সম্পর্কিত বিষয়:
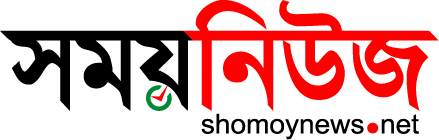


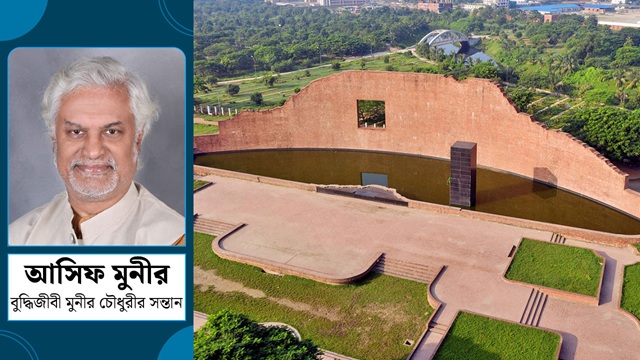

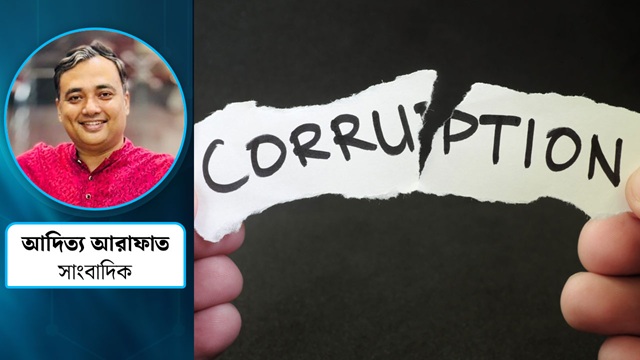





আপনার মূল্যবান মতামত দিন: