বৈষম্য বিলোপের বাজেট হোক
প্রকাশিত:
২১ মে ২০২৫ ১৪:৩৮
আপডেট:
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ০৩:৪৫

বাংলাদেশে কয়েক দশকের রাজনৈতিক অর্থনীতির কুফল হলো, সমাজে তৈরি হওয়া চরম বৈষম্য। যার সর্বশেষ ফলাফল, সরকারি চাকরিতে বৈষম্যের শিকার হয়ে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সময় এসেছে নতুন বাজেট ঘোষণার। জুনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা হবে। এবারের বাজেট কেমন হওয়া উচিত, এ নিয়ে আছে নানা আলোচনা পর্যালোচনা। তবে মোটা দাগে বলা যায়, যে বৈষম্যকে কেন্দ্র করে দেশে গণঅভ্যুত্থান হয়ে গেল, এবারের বাজেটের তাৎপর্য হওয়া উচিত তা বিলোপে চেষ্টার সূচনা করা।
বাজেট একটি সরকারের রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের আর্থিক পরিকল্পনা। অন্তর্বর্তী সরকার যেহেতু রাজনৈতিক সরকার নয়, তাই বৈষম্য বিলোপে যেসব আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বাধা আছে তা সহজে অতিক্রম করা সম্ভব। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এবারের বাজেটে বৈষম্য বিলোপে নেওয়া যেতে পারে কিছু নীতি কৌশল। যার মধ্যে থাকতে পারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কর ন্যায্যতা ও সুষম উন্নয়ন বরাদ্দ। এছাড়া সরকার পরিচালনায় আগে যেসব অযাচিত ব্যয় হয়েছে তার লাগাম টেনে ধরারও সময় এসেছে।
বৈষম্য পরিমাপের আন্তর্জাতিক সূচক হলো জিনি কিংবা গিনি সহগ। এই সহগ ০ থেকে ১ কিংবা ১০০ তে হিসাব করা হয়। সহগ যত ১ বা ১০০ এর কাছাকাছি যাবে বৈষম্য তত বাড়ে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ২০১০ সালে যেখানে জাতীয় পর্যায়ে গিনি সহগ ছিল ০.৪৫৮ তা বেড়ে ২০২২ সালে হয়েছে ০.৪৯৯। গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। তবে গ্রামের তুলনায় শহরে তীব্র হচ্ছে। ২০১০ সালে শহরের জন্য গিনি সহগ ছিল ০.৪৫২, তা ২০২২ সালে এসে বেড়ে হয়েছে ০.৫৩৯। এই সহগ জাতীয় সহগের চেয়ে অনেক বেশি। শহরে বৈষম্য তীব্র হওয়ার বড় কারণ সম্পদের অসমবণ্টন। এখানে ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে আয় ও সম্পদের যে পার্থক্য তা গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। (Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2022)
বৈষম্যের কারণ
সমাজ বা রাষ্ট্রের একটি অংশ সব সময় রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে। এই সংযোগ তাদের বাড়তি সুবিধা দেয়। এই প্রবণতা তখনই বাড়ে যখন রাষ্ট্রে সুশাসনের ঘাটতি হয়। আবার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতা সুসংহত করতে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীও তৈরি করে। এরা নানা সুযোগ সুবিধা নেয়। যেমন-সরকারি চাকরিতে প্রবেশ, টেন্ডার বাণিজ্যে অগ্রাধিকার, ট্যাক্স ফাকি, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া, ঋণ পুনরায় তফসিল করা, সেই ঋণ বিদেশে পাচার করা ইত্যাদি। নানা অবৈধ উপায়ে এসব অর্থের প্রবাহ সামাজিক কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের নিচের দিকেও যায়। যেমন-ক্লাব, সমিতি, খেলার আয়োজন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এসবের বাহক।
ফলে সমাজের একটা অংশের হাতে গেল দেড় দশকে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় প্রচুর অর্থ এসেছে। এই অর্থ যখন বাজারে প্রবেশ করেছে তখন বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। এই যে সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি হয়েছে, তারা যে সম্পদ কুক্ষিগত করেছে তা নিশ্চয়ই কারও না কারও পকেট থেকেই গিয়েছে। ফলে বিপরীতে আরেকটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে যারা বঞ্চিত। এই বঞ্চনা তাদের দুই দিক থেকে চেপে ধরেছে। প্রথমত আয় বা সম্পদ কমে যাওয়া, আর দ্বিতীয়ত মূল্যস্ফীতি তথা জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়া। এই দুইয়ে মিলে তারা আরও দরিদ্র হয়েছে। যে কারণে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বলছে, নতুন করে বাংলাদেশে ৩০ লাখ মানুষ দরিদ্র হতে পারে।
পারস্পরিক যোগসাজশে তৈরি হওয়া দুর্নীতি থেকে উদ্ভব হয়েছে সুযোগের বৈষম্যও। যেমন ধরা যাক একটি সেতু নির্মাণে যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে সেখানে সবচেয়ে কম দর ডাকা প্রতিষ্ঠানটি কাজ পায়নি। পেয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে উপর মহলের যোগাযোগ ভালো ছিল। এতে করে রাষ্ট্রীয় অর্থের লুটপাট, অপচয় যেমন হয়েছে তেমনি যে প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা হয়ে বাদ পড়লো, সেটি সুযোগের বৈষম্যের ভুক্তভোগী। সরকারকে তাই সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে।
বাজেটে করণীয়
বৈষম্যের এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে যে সুযোগ আছে তা কাজে লাগানো উচিত। বাজেটে সরকারগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করে মানুষের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানো। কারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে বেশি দূর আগানো সম্ভব নয়। তবে বর্তমান সরকার যেহেতু দীর্ঘমেয়াদি সরকার নয় তাই বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা কম। এর সাথে আছে তীব্র জ্বালানি বিশেষ করে গ্যাস সংকট।
এজন্য সরকারের উচিত হবে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান তৈরির চেয়ে, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দিকে বেশি জোর দেওয়া। প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টার সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফর তারই অংশ বলা যায়। তবে মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় অভিবাসন ব্যয় প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশি। নতুন বাজেটে এই খরচ কমিয়ে আনার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা চাই।
এছাড়া রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এর পরিমাণ বাড়াতে পারলে ভালো। প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানো উৎসাহী করার উদ্যোগ নিতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দুবাই সফর করে সেটি কারার চেষ্টা করেছে। তবে এই উদ্যোগ আরও বাড়াতে হবে। এছাড়া রেমিট্যান্সের অর্থ দেশে যেন শুধু বাড়ি-ঘর তৈরি, জমি কেনা কিংবা ভোগে ব্যয় না হয়ে যায় সেদিক খেয়াল রাখা। এজন্য উৎপাদনশীল খাতে রেমিট্যান্সের অর্থ ব্যয় করতে নতুন বাজেটে উদ্যোগ চাই। এতে বৈষম্য কমে আসবে।
প্রশ্ন আসতে পারে রেমিট্যান্স আবার কীভাবে বৈষম্য তৈরি করে? ধরুন একই পরিবারের দুই ভাই একজন কৃষি কাজ করেন, অন্যজন প্রবাসী। যিনি কৃষি কাজ করছেন তিনি তার উৎপাদিত পণ্যের দাম পাচ্ছেন না। আর, যিনি প্রবাসী, প্রতি মাসে পরিবারের জন্য টাকা পাঠাচ্ছেন। পরিবারের সদস্যরা সেই টাকা সংসার চালাতে ব্যয় করছে। কিন্তু কৃষি কাজ করা ভাইয়ের পরিবার চাইলেও ওই পরিমাণ ব্যয় করতে পারছে না। কিন্তু প্রবাসীর অর্থ যদি ভোগ ব্যয়ের পাশাপাশি বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকতো তাহলে কর্মসংস্থান তৈরি হতো। সেখানে ওই কৃষকের ছেলে কাজ করে আয় করতো। এতে দুই পরিবারের মধ্যে আয়ের একটি সমতা তৈরি হতো। তাই রেমিট্যান্সের অর্থ উৎপানদশীল, বিশেষ করে কৃষি ভিত্তিক শিল্প উৎপাদনে কাজে লাগানোর বাজেট প্রস্তাবনা থাকতে পারে।
আগেই বলেছি, সুযোগের সমতার তীব্র সংকটে ভুগছে দেশ। শোনা যাচ্ছে, বাজেটে বেকার ভাতার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। এটি না করে, বরং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে বাজেটে। যাতে তরুণরা উদ্যোক্তা হতে পারে। এটি দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, তবে এই বাজেটে তার সূচনা হতে পারে।
বৈষম্য কমানোর আরেকটি উদ্যোগ হলো, পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়ানো। সহজ করে বললে, ভ্যাট কমাতে হবে। কারণ বাজারে গিয়ে যিনি লাখ টাকা আয় করেন তিনি একটি পণ্য কিনতে গিয়ে যে ভ্যাট দেন, যিনি ১০ হাজার টাকা আয় করেন বা তার কম তিনিও একই হারে ভ্যাট দেন। এটা কখনোই কর ন্যায্যতা হতে পারে না।
এবারের বাজেটে তাই সরকারকে কর ন্যায্যতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য যাদের সম্পদ বা আয় বেশি তাদের কাছ থেকে বেশি কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। করযোগ্য অনেকেই আছেন তারা কর দিচ্ছে না, তাদের থেকে আদায় বাড়াতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে করফাঁকি বন্ধ করতে। এই একটি কাজ এক দিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াবে অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের চেহারাও পরিবর্তন করবে। কারণ করফাঁকি বন্ধ করতে গিয়ে সরকারকে বিভিন্ন খাতে সংস্কার করতে হবে, যার সুফল বাণিজ্যে পড়বেই।
নতুন বাস্তবতায় সময় এসেছে সরকারি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরা। আগে যেহেতু প্রশাসনকে খুশি রাখতে বহু ব্যয় সরকারকে করতে হয়েছে, বর্তমান সরকারের সেই পিছুটান নেই। তাই এবারের বাজেটে এই ব্যয় কমিয়ে আনা যায়। এতে বাজারে টাকার প্রবাহ কমে মূল্যস্ফীতিও কমবে।
আর বরাদ্দের দিক থেকে নতুন অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের শিক্ষালয়ে ফেরত পাঠাতে হলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা প্রয়োজন। এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যয় বাড়াতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে এর প্রস্তুতির জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা উচিত। আর, গণঅভ্যুত্থানে আহত ছাড়াও সব ধরনের জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত করতে এবারের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা উচিত।
ফরহাদ হোসেন ।। গণমাধ্যমকর্মী ও সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, ইআরএফ
[email protected]
সম্পর্কিত বিষয়:
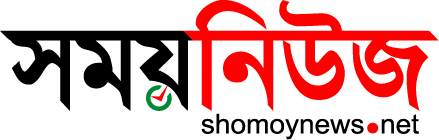


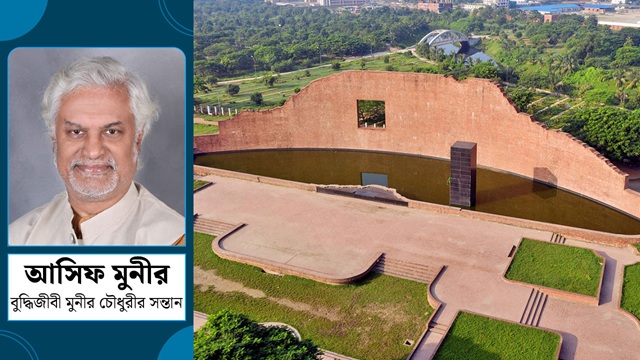

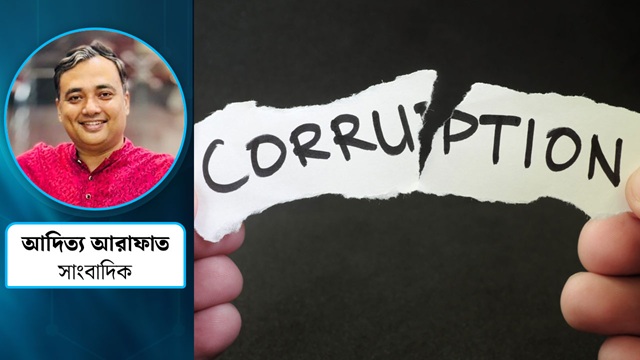





আপনার মূল্যবান মতামত দিন: